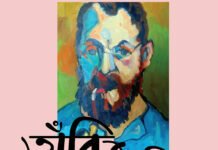ধরেন জীবনানন্দ তার কবিতার খাতাগুলোর সাথে আরো কয়েকটা খাতাও রেখে গেছেন। সেইসব খাতায় কোন কবিতা দিয়ে কী বোঝাচ্ছেন তা লেখা। কী ঘটত তখন? অনুমান করা যায়, যাদের কোনো কবিতা নিয়ে কোনো কনফিউশন হবে, তারা সাথে সাথে নির্দিষ্ট পেইজে গিয়ে পড়ে নিতে পারতেন কবির ভাবনা। তখন কবিতাটাকে সহজে বুঝতে পারা যেত। কথা সত্য। কিন্তু একটা কবিতার নানান পাঠকের কাছে নানান রকমভাবে হাজির হবার যে-সম্ভাবনা, তাও তো নষ্ট হয়ে যেত, না? সব পাঠকই তখন কবির দেখানো অর্থেই কবিতার মানে খুঁজতেন। যার যার অভিজ্ঞতা-পরিবেশের সাথে মিলিয়ে পড়ার যে-আনন্দ তা থেকে বঞ্চিত হতেন অনেকেই। একই বিষয় বোধহয় অন্যান্য অনেক আর্টের বেলায়ও খাটে। তবে নির্দিষ্ট একটা অর্থ তৈরি করে, মানে শিল্পী ও দর্শক/পাঠক দু’পক্ষের জন্য একই অর্থের, এমন শিল্পও কম নেই। বেশিরভাগ সময় অই ধরনের শিল্পের মানে নিয়ে বিতর্কও কম। আমার এই এক না করার দিকেই আগ্রহ। এ-আগ্রহের কারণেই, কী বলতে চাচ্ছি তার বদলে কিভাবে বললাম এবং কেন অইভাবে বললাম তা বলতেই আগ্রহ বোধ করছি। ধারণা করতেছি, এই কীভাবে এবং কেন’র উত্তর দিলে যারা আমার আর্ট ‘বুঝতে’ কিছুটা অন্তত কৌতূহলী, তারা পথ না পেলেও মানচিত্রের হদিস কিছুটা পাবেন।
আর একটা বিষয়, আমরা যেহেতু কার্যকারণের দুনিয়ায় বাস করতে পছন্দ করি, তাই আর্টকেও অইভাবে দেখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কিন্তু আর্টতো বিজ্ঞান নয়। তাই লজিক/রিজনের এন্টেনায় তাকে সবসময় ধরা কঠিন তো বটেই। অসাধ্যও অনেকসময়। সবচেয়ে ভালো, যুক্তিমনস্কতাকে যদি অন্য কোথাও রেখে আর্টকে দেখতে পারি।
শুরুর অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করি।
তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। এখানে সিলেবাসটা এমন ছিল, থার্ড ইয়ার পর্যন্ত বাস্তবতা-নির্ভর ছবি আঁকার কৌশল শিখতে হতো। বাস্তবতা-নির্ভর বলতে চোখে যা দেখি, তেমন করে আঁকা অনেকটা বা বলা যায় ফটোগ্রাফিক বাস্তবতার মতোন ছবি। যেটা আমরা আমাদের উপনিবেশজাত শিক্ষাব্যবস্থা মারফত পাই। তো থার্ড ইয়ারের পর ব্যবস্থাটা ছিল এমন, যে যার মতোন করে আঁকতে পারবে। মানে কেউ চাইলে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা-নির্ভর যে-ছবি অইরকমও আঁকতে পারবে আবার চাইলে ভিন্ন কিছুও। তবে স্টাডি (প্র্যাকটিসের জন্য করা হয়) না। ক্রিয়েটিভ পেইন্টিং হতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা এমন বা আশপাশের পরিবেশ আমাদের মধ্যে শুধু ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা-নির্ভর ছবি পছন্দ করার রুচিই নির্মাণ করে। ভিতরে ভিতরে। নানানভাবে। এই নির্মাণের ফলে যেটা হয় আমরা ভালো শিল্প বলতে অই স্কিল-নির্ভর ছবিকেই শুধু বুঝি। চারুকলার এ তিন বছরের পড়াশোনাও অই দিকেই পথ দেখায়। বাইরের লোকজন তো বটেই, খোদ চারুকলার পড়ুয়ারাও অই দিকেই আগায়। আমিও আগাইলাম। চারুকলার এই ফোর্থ ইয়ারটা যারা আঁকতে চায়, না আঁকতে চাইলেও মানে শুধু পাশের জন্য পড়তে চাইলেও বেশ ক্রুশিয়াল টাইম। ক্রুশিয়াল এই কারণে, খাঁচার পাখি, যে উড়তে অভ্যস্ত না, তার খোলা আকাশের নিচে পড়ে বিহব্বল হবার মতোন অবস্থা এটা। কারণ পড়তে পড়তে সিলেবাসের কারণে সে ইউরোপিয়ান স্কিল শিখলেও, এর বাইরেও নানান কিছু দেখে। সে মুঘল মিনিয়েচার যেমন দেখে, সে লুসিয়ান ফ্রয়েডও দেখে। ফ্রান্সিস বেকন দেখার পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথের পেইন্টিংও দেখে। দেখে পিকাসোর কিউবিজমের সাথে সাথে শাগালের উড়তে থাকা মানুষ। এত এত ধরন দেখার কারণে এবং প্রথম তিন বছর মোটেও চিন্তানির্ভর কিছু আঁকতে না হবার কারণে, তারা দিশকুল হারায় ফেলে। এই হারানো দিশকুলের হাওয়ায় পাল তুলে দেয় কী আঁকবে অই চিন্তাও। দুইটা চিন্তার ডুয়েল শুরু হয় তখন: কী আঁকবে আর কিভাবে আঁকবে। কিভাবে আঁকবে তার সমাধান হিসাবে আসে তিন বছরের স্কিল প্র্যাকটিস। মানে আলোছায়া-পার্সপেক্টিভসহ ফটোগ্রাফের মতোন করে আঁকা। এই আঁকার ধরনটির নাম নিয়ে ভাষাগত একটু জটিলতা আছে। এটা ‘রিয়েলেস্টিকভাবে আঁকা’ বলে থাকে সবাই। কিন্তু এই ‘রিয়েল’-এর একক মালিকানা সবাই এই স্কিলকে দিতে চায় না। তারা বলেন, এই রেটিনা-নির্ভর ছবির বাইরেও তো আরো নানান রিয়েলিটি আছে, তাদের কী হবে! কথা মিথ্যা নয়। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এইরকম ছবির আঁকার স্কিলটাকে আমরা রেটিনা-নির্ভরতাও বলতে পারি। যেখানে সচরাচর বুদ্ধির গুরুত্ব কম থাকে। এখানে ‘সচরাচর’ শব্দটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। নাহলে আমার বক্তব্যকে ‘ঢালাও’ বলার একটা আশংকা তৈয়ার হতে পারে। আরো একটা একাডেমিক জটিলতার কথা বলার দরকার আছে এখানে। ক্লাসে সাধারণত একটা ছবি আঁকলে হয় না। ক্লাস অনুযায়ী, কোর্স অনুযায়ী একটার পর একটা আঁকতে হয়। পরম্পরা থাকতে হয়। এইটাকে ‘সিরিজ’ বলে ডাকা হয়। তাই দুম করে বা দুর্ঘটনাবশত একটা দুইটা ‘ভালো’ ছবি মানে শিক্ষক-মর্জিমাফিক আঁকা গেলেও নিয়মিত এই মর্জি খুশি করাটা কঠিনই আসলে। আর মনে হয় এই কারণেই শিক্ষকরা এই ‘সিরিজ’ পদ্ধতিটা ফলো করে থাকেন।


এইভাবে ‘সিরিজ’ এঁকে যাওয়ার জন্য ছাত্ররা একটা বিষয় ঠিক করে। পরে অই ‘বিষয়’ নিয়ে আগায়। মানে অই ‘বিষয়টা’কেই পর পর এঁকে যায়। যেটাকে সিরিজ বলেছি আমি। তো এই ‘বিষয়’ নির্ধারণও একটা সমস্যা। সমস্যা এজন্য, ছাত্ররা তখন ক্ষমতা-কাঠামো, আত্মানুসন্ধান, হারানো ঐতিহ্য ইত্যাদি নানান টপিক ঠিক করে অই টপিককে সিম্বলাইজ করে এমন জিনিসকে পেইন্টিংয়ের সাবজেক্ট বানায় আঁকতে থাকে। এখন কেউ যদি ক্ষমতার সিম্বল হিসাবে ‘চেয়ার’ আঁকতে থাকে, সে কতরকম পেইন্টিং করবে এই এক চেয়ার নিয়ে। এক চেয়ার আর কতবার আঁকা যায়! তখন ক্লিশে হয়ে যায় ছবিগুলো। আর্টিস্টও বোর হন। বেশি আর আগাইতে পারেন না। তো এই গ্যাঁড়াকলে যখন পড়লাম, আমি প্রথমেই আঁকার টুল হিসাবে নিলাম ‘মানুষ’কে। মানে হিউমান ফিগার। যে-বিষয়েই আঁকি না কেন, হিউম্যান ফিগার ভিত্তি করেই আঁকবো। এটা একটা ভালো সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ, চেয়ার-টেবিল এরকম বিষয় ধরে আঁকা শুরু করলে, তাতে বেশিদূর আগানো যাইতো না। তাছাড়া একটা হিউমান ফিগারের যে ভেরিয়েশন তা অন্য কিছুতে অতটা নাই। তো ফিগার আঁকবো ঠিক করলেও, অই ফিগার কিভাবে আঁকবো ভাবতে ভাবতেই, ক্লাসের ঠেলায় কয়েকটা ছবি এঁকে ফেললাম। তখন বাম রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তাই এর প্রভাবও ছিল এই আঁকার বিষয়ে। তথাকথিত ‘সমাজ বাস্তবতা’কে তুলে ধরার দায়। একদিন, এক ক্লাসে তখনকার শিক্ষক-শিল্পী মনসুর উল করিম স্যারকে কাজগুলা দেখাচ্ছিলাম। অইখানে একটা ছবি ছিল এমন; একটা ইলেকট্রিকের খুঁটির নিচে একটা মেয়ে দাঁড়ায় আছে। মেয়েটা প্রস্টিটিউট। মোটামুটি স্কিলে আঁকা ছবিটা। খামতি ছিল অনেক। অই অদক্ষতা নিয়ে উনি কিছু বললেন না। উনি বললেন, এই যে মেয়েটা, তার জীবন সম্পর্কে তো তুমি জানো না। ওর সাফারিংস তো ওর। তুমি তোমাকে আঁকো। তোমার নিজের চারপাশটা আঁকো। কথাটা মনে ধরল। আসলেই তো একজন প্রস্টিটিউট সর্ম্পকে আমি আর কতটুক জানি। সিনেমা প্যালেসে, সিপিবি অফিসের আগে ওদের জটলা-ঝগড়াঝাটি করতে দেখা বাদে। আর যতটুক জানি তা এইখানে-অইখানে এটা-অইটা পড়া মারফত। এমনও না যে আঁকার আগে এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আসতে হবে বা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সই আঁকতে হবে। কিন্তু সমাজের এরকম পেশার যারা, বা অন্য লিঙ্গ পরিচয়ের যারা তাদের আর্টে আনতে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের ‘আদার’ করে রাখার ব্যাপার আছে। এনজিওপনা আছে। যেইটা চাচ্ছিলাম না ঠিক। তো একটা ওয়ে খুঁজতেছিলাম। তখন ওয়ে আউট হিসাবে কিছু ডিজাইনধর্মী পেইন্টিংও ট্রাই করছিলাম। কিন্তু অইগুলা স্রেফ ডিজাইনই ছিল।পেইন্টিং হয় নাই। এসময়ই চারুকলার লাইব্রেরিতে (তখন ইন্টারনেট সুলভ ছিল না এতটা) পরিচিত হই ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট ডুবুফের সাথে। যিনি বাচ্চাদের আঁকা এবং আউটসাইডার আর্টের (যদিও এই টার্মটা সমস্যাজনক একটু) দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড ছিলেন। উনি বাদেও এরকম আরো বেশ কিছু আর্টিস্টের সাথে পরিচিত হই। বিল টেইলর এমন একজন। উনাদের আঁকা দেখে মনে হইল স্কিলকে দূরে রাখতে পারলেই মনে হয় ভালো। এর একটা সুবিধা এই, ধরেন একটা ছবি খুব স্কিলফুলিই আঁকা হইল। সব ঠিকঠাক। শুধু আপনি একটা আঙুলের ড্রয়িংয়ে একটু গোলমাল করে ফেলছেন। সাথে সাথেই পুরা কাজটা ইমব্যালেন্সড হয়ে যাইতে পারে। সুবিধা যেটা স্কিলে না থাকার, ফ্রিডম অনেক বেশি পাওয়া যায়। আপনার ভুল হওয়ার কোনো সুযোগই নাই। আঙুল ছয়টা দিলেও সমস্যা নাই। তিনটাও দিলেও না। শাগালের একটা পেইন্টিংয়ে এরকম ছয়টা আঙুল আছে। দেখলে অস্বাভাবিক মনে হবে না। আরেকটা বিষয়, ধরেন আপনি একটা কবিতা লিখলেন। দেখে বললাম, বাহ্ আপনার হাতের লেখা তো সুন্দর। অর্থাৎ লেখার সৌন্দর্যের জন্য কবিতার দিকে মনোযোগই গেল না। এইটাই সমস্যার। রেটিনা নির্ভর পেইন্টিংয়েও এ-সমস্যাটা হয়। স্কিলটা এত গুরুত্ব পায়, ছবির বিষয়ের দিক থেকে মনোযোগ সরে যায়। মানে এটা ঘটে। তবে এই ঘটাটা সার্বজনীন না। বিকাশ ভট্টাচার্যের পেইন্টিং বা লুসিয়ান ফ্রয়েডে এটা ঘটবে না। কারণ, উনাদের কাজে স্কিলটা মুখ্য হয়ে উঠে নাই। উনারাই চান নাই। আমিও চেষ্টা করতে লাগলাম কিভাবে স্কিলটাকে স্কিপ করা যায়। দেখলাম পারতেছি। তখন বাচ্চাদের পড়াইতাম। তারাও আমাকে ইনফ্লুয়েন্সড করেছে। তাদের আঁকার ধরনে যেমন, ইমাজিনেশনও। মনে আছে একবার আমার এক ছাত্র একটা লোকের ছবি আঁকলো। লোকটা আম পাড়তেছে। হাত অনেক লম্বা। কেন? তার উত্তর: হাত ছোট আঁকলে আম পাড়বে কিভাবে! কঠিন যুক্তি! আরেকটা ঘটনা, সুধীর চক্রবর্তীর কোনো একটা লেখায় পড়ছিলাম। গ্রামের একজন আর্টিস্ট, স্বশিক্ষিত; ছবি আঁকতেছেন গাছের। গাছটার উপরে ফলফুলপাতা ইত্যাদি যেমন আছে, তেমন মাটির নিচের শেকড়-বাকড়ও দেখা যাচ্ছে। সুধীর চক্রবর্তীর সাথে তখন একজন একাডেমিক আর্টিস্ট। শেকড়-বাকড়ের ব্যাপারটা উনি মানতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন গ্রামের অই শিল্পীকে, শিকড় কেন দেখা যাবে! মাটির নিচে থাকবে না! কিন্তু শিকড় তো আছে, না? – গ্রামের শিল্পীর সরল উত্তর। এখানেই পার্থক্যটা। আমরা উপনিবেশজাত শিল্পীরা, যেখানে চোখের দেখার লজিককে একমাত্র ধরে নিয়েছি, সেখানে এই গ্রামের শিল্পীদের লজিক একমাত্রিক না। তো বাচ্চাদের এই আঁকার ধরন অনুসরণ করে অই সময় অনেকগুলো পেইন্টিং করি। এই আকাঁর ধরন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে। আমি এর আগে প্রচুর ওয়াটার কালার করেছি। ড্রয়িংও। আউটডোরে। স্কিল কিছুটা হলেও আয়ত্ব করেছি। এই স্কিল বাদ দিয়ে হঠাৎ করে এরকম আঁকা শুরু করাতে, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা, তারা হতাশ হলেন খুব। মনে করলেন, ভুল পথে আগাচ্ছি। আর যারা, তারা অপেক্ষা করতেছিলেন, শেষমেষ কী হয় দেখার জন্য। তাছাড়া তখন আঁকতাম কাগজে। তার উপর কালি, প্যাস্টেলে। কাগজে আঁকার কারণ ছিল, এতে সস্তায় কম সময়ে প্রচুর কাজ করা যায়। ক্যানভাসেও দ্রুত করা যায়। কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ বেশি। কয়েকশ টাকার একটা ক্যানভাস আধাঘণ্টায় শেষ হয়ে গেলে, এক-দু সপ্তাহের একটা ক্লাসের জন্যতো ভালোই সমস্যা, না? সময় ও অর্থ দুদিক থেকেই। কাগজে করতে থাকার কারণে সবচে বড় সুবিধা হল, অল্প সময়েই যেহেতু কয়েকটা করে ফেলা যায়, ইমপ্রুভমেন্টটাও দ্রুত হয়। নষ্ট হবার ভয়ও নাই। ক্যানভাসে করলে পছন্দ না হলে মুছে করতে হয়। এই মুছার ব্যাপারটা নানানভাবে ক্ষতি করে। কনফিডেন্স কমায় দেয়। আর মুছার যে ঝক্কি, হ্যাপা। তা আঁকার স্বতঃস্ফূর্ততাকেও কমায় দেয়। ফলে প্রোগ্রেসটাও বেশ ধীরে ধীরে হয়।

বলা উচিত, বাচ্চাদের ছবি, আউটসাইডার আর্টিস্ট এদের পাশাপাশি মার্কেজ-শহীদুল জহির-আমোস টটুওলা মতোন লেখকরাও আমাকে প্রভাবিত করতে থাকে তখন। মনে আছে ফোর্থ ইয়ারেই স্বাতী ম্যাম নিঃসঙ্গতার একশ বছর পড়তে দিয়েছিলেন। শহীদুল জহিরও প্রথম পড়া শুরু করি তখনই। ফলে, তাদের কল্পনার যে-বিস্তৃতি, বিশেষ করে শহীদুল জহিরের বলার যে ধরন অইটা আমাকে আরো ইচ্ছামতোন আঁকতে সাহস যোগাইতে থাকে তখন। পরে বুঝি, শুধু যে এইসব ফর্মাল ইনফ্লুয়েন্সই ছিল তা না, ছোট থেকে মা-ঠাকুরামার মুখে শোনা নানান গল্প, প্রতিমা-ক্যালেন্ডারে দেখে আসা দুর্গার দশ হাত, রাবণের দশ মাথা কিংবা গণেশের হাতির মাথা-চার হাতের মতোন ইমাজিনেশনের প্রভাবও আমার কাজে আছে। প্রভাব থাকবে এরাবিয়ান নাইটস-এরও। হাই স্কুলে আমাদের সমাজ পড়াইতেন এক হুজুর স্যার। তিনি প্রায় প্রত্যেকদিনই ক্লাসের পড়া দশ মিনিট আগে শেষ করে দিতেন। তারপর এই শেষ দশ মিনিট আরব্য রজনীর গল্প শোনাইতেন। অল্প অল্প করে। মাঝে মাঝে এমন একটা সময় ঘণ্টা বাজতো! পরের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। তখনো বিটিভির প্রতি শুক্রবারের সিরিয়ালটা আসে নাই। সিরিয়াল যখন আসল তখন আরো রমরমা অবস্থা। তো আজকে লিখতে লিখতে মনে হইল, আমার মানস গঠনে এই চেরাগের জ্বিন-চল্লিশ চোরের প্রভাবও নিশ্চয়ই আছে।
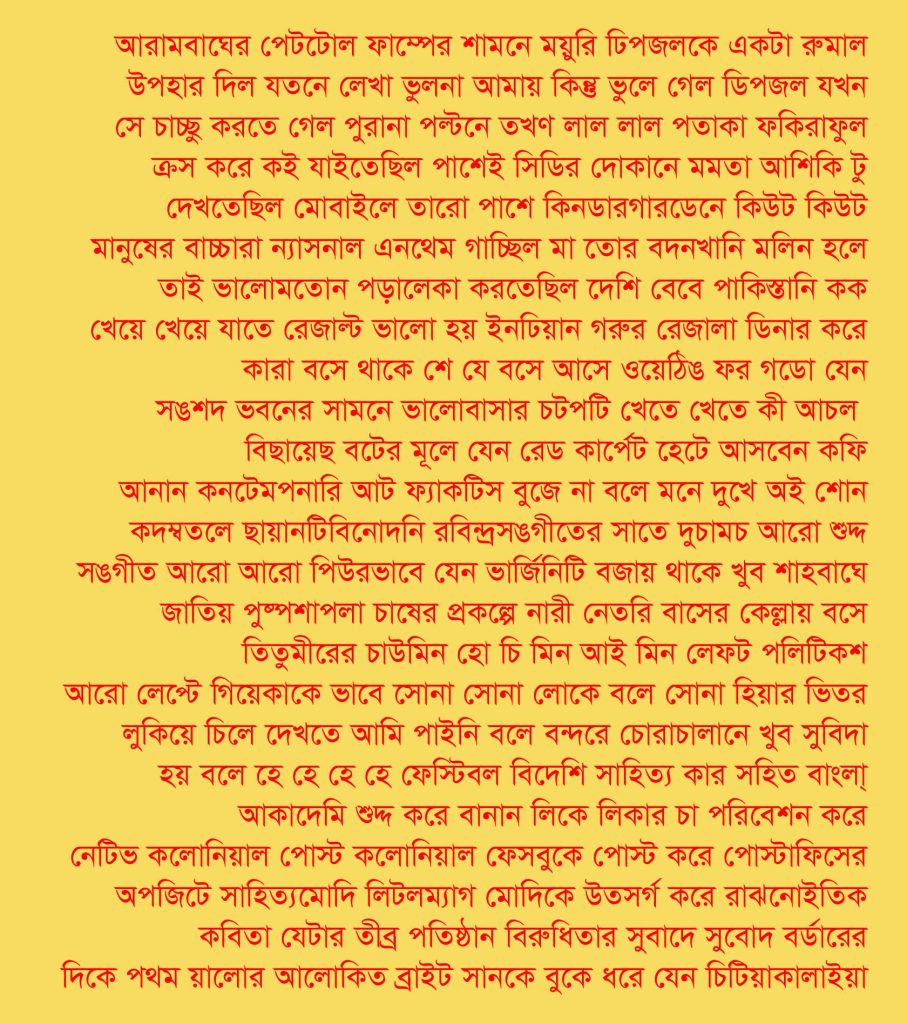
এই করতে করতে ফোর্থ ইয়ার কমপ্লিট হয়ে গেল। পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট পাওয়ার পর দেখলাম, আমার ক্যানভাস এবং বাস্তবতা-নির্ভর আঁকিয়ে বন্ধুরাই ভালো মার্কস পাইছেন। বুঝলাম, আমার এই পন্থা বেশিরভাগ শিক্ষকদের কাছেই কনফিউজিং, সিরিয়াস কিছু না। ধারণা করি, কাগজে আঁকাটাকে তারা আমার ক্যানভাসে আঁকতে না পারার অসমর্থতা হিসাবেই বেশি নিয়েছিলেন।


এরপর এম. এ. শুরু হইল। এই ক্লাসে একটা কোর্স ছিল এমন, বড় কোনো শিল্পীর কম্পোজিশনকে ফলো করে আঁকতে হবে। তো কারে ফলো করি! ভাবতে ভাবতে নিয়ে নিলাম ডেভিড হকনির একটা পেইন্টিং। অইটার মতোন করে, ড্রয়িং-কোলাজ করে একটা কাজ দাঁড় করাইলাম। যুবরাজ স্যারের ক্লাস ছিল অইটা। উনি এপ্রিশিয়েট করলেন। আগ্রহ পাইলাম। পরের ক্লাসগুলাতে আরো কয়েকটা একই ধাঁচের কাজ করলাম। একেকটা কোর্স একেকজন টিচার পড়ান। তো পরে, আরেকটা কোর্সের ক্লাস নিতে আসলেন, মনসুর উল করিম স্যার। যেইখানে কাজ করতেছিলাম, তার পাশেই ছিল ডেভিড হকনিকে ফলো করে আঁকা ছবিটা। উনি ক্লাসে আসতেন প্রায় নিঃশব্দে। এরকম একবার এসে আমার পিছনে দাঁড়ায় পাশের ছবিটা দেখতেছেন। খেয়াল করি নাই। আমি আমার কাজ করতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন খেয়াল করলাম, উনিই আগে কথা বললেন, এটা তোমার? হ্যাঁ বললাম। উনি কিছুই বললেন না। বাকিদের কাজ দেখে চলে গেলেন। পরে আবার যখন আসলেন, জিজ্ঞেস করলাম, স্যার কেমন হয়েছে? বললেন পোস্টার-পোস্টার লাগতেছে। পোস্টার তখনো আমার কাছে ছোট মানের আর্ট। তাই মর্মাহত হইলাম। উনারে তো পছন্দ করি। কিন্তু মন্তব্যটা মানতে পারলাম না। মনে হইল উনিও মানতে পারেন নাই আমার এই রকম ছবি আঁকার ধরণ। উনি আমার ড্রয়িংয়ের তারিফ করতেন। উনি ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট সুনীল দাসের কথা বলতেন। বলতেন সুনীল দাস এত ঘোড়ার ছবি আঁকছেন, উনারে ঘোড়া সুনীল বলা হইতো। আরো বলতেন উট-মুঠ-ঘোট আঁকার কথাও। মানে উট, হাতের পাতা (নানান ভঙ্গিমায়) এবং ঘোড়া আঁকলে পরে ড্রয়িং ভালো রপ্ত হয়। বলতেন এনিমেল স্টাডির কথা। হিউম্যান ফিগার স্টাডির কথা। আমি উট-ঘোড়ার সুযোগ না পাইলেও, প্রচুর হিউমান ফিগার আর মোষ স্টাডি করেছি। তখন বটতলীর পর দেওয়ান হাট ব্রিজের নিচে অনেকগুলো মোষ বাঁধা থাকতো। সকালে সাড়ে ছয়টা/সাতটার দিকে অইখানে চলে যাইতাম, সেকেন্ড ট্রেনের (সাড়ে আটটায়) আগে পর্যন্ত থাকতাম। আর যাইতাম বিকেলে, ক্যাম্পাস শেষে। এইভাবে অনেকদিন আঁকছিলাম। নিষ্ঠা সহকারে। এই ড্রয়িংগুলো করে প্রায় নিয়মিতই দেখাতাম মনসুর উল করিম স্যারকে। উনি নানান পরামর্শ দিতেন। বলতেন সমস্যাগুলা এবং আরো কী কী করা যায়। তো এত কিছুর পর উনার (আরো অনেকেরও) ভাবা স্বাভাবিক ছিল আমি লাইনে থাকবো। কিন্তু থাকি নাই। আফসোস! তবে অই সময়ের অই স্টাডি পরে নানানভাবে হেল্প করেছে। বিশেষ করে ইলাস্ট্রেশন করতে গিয়ে। যাই হোক, মনসুর উল করিম স্যারের পর আরেকটা কোর্স নিতে ঢালী আল মামুন স্যার আসলেন। একই ক্লাসরুমে। অই পেইন্টিংটা উনারেও দেখাইলাম। উনিও এপ্রিশিয়েট করলেন। বললাম, স্যার মনসুর স্যারতো এইরকম বললেন। উনি চুপ করে ছিলেন একটু। পরে বললেন, কেন পোস্টার কি তোমার পছন্দ না? তখন আমি ফ্রিজের বক্সের যে কার্টুন অইগুলাতেও আঁকি। এই বক্সের উপরের কাগজের যে-আবরণ অইটা ছিঁড়ে ফেললে একরকম টেক্সচার আসে। অইটার সাথে সাথে কোথাও কোথাও পত্রিকাও ইউজ করি। পত্রিকার টেক্সটের কারণে যে লুক, অইটার জন্যই মূলত। তো এইরকম একটা কাজ দেখে মামুন স্যার বল্লেন, এই পেপারগুলো কেন? পেপারের টেক্সটের সাথে কাজের কোনো সর্ম্পক আছে? বললাম নাই। সাথে আমার কারণটাও বললাম। উনি বললেন, ধরো টেক্সটগুলোও তোমার পছন্দ মতোন হলে, কাজের আরেকটা মাত্রা আসবে না? একমত হইলাম। পরে অইভাবেই ইউজ করার চেষ্টা করতাম। অবশ্যই টেক্সট আমি আরো আগে থেকেই লিখতাম। কিন্তু শুধু টেক্সচার হিসাবে পরে আর রাখি নাই।


এসব বাক্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাহিত্যিক কনটেক্সটের সাথে কানেক্ট করে বটে, তবে মোটাদাগে অর্থহীন। পুরোপুরিই। কারণ কী? প্রথমত আমাদের যে অভ্যস্ততা-আর্কষণ, একরকম পবিত্র ভক্তিও আছে শুদ্ধ বানান-বাক্যের প্রতি, তাকে বিশৃঙ্খল করা। অর্থপূর্ণতা-লজিক-রিজনের প্রতি আধুনিক যে বিশ্বাসব্যবস্থা, তার প্রতি অবিশ্বাসই এইসব পোস্টার-লিফলেটের মূল প্রণোদনা।
এখানে আরেকটা বিষয় বলা দরকার, ফোর্থ ইয়ারেই আরেকটা কোর্স ছিল, মাস্টারপিস পেইন্টিং ম্যানিপুলেশন। কোনো একটা মাস্টারপিসকে নিজের কনটেক্সটের সাথে মিলায় আঁকতে হতো। আমার তখনো এবং এখনো বিষয়টা ইন্টারেস্টিং মনে হয়। এই ইন্টারেস্টিং লাগার কারণে পাশ করে ফেলার এত বছর পরেও ম্যানিপুলেট করি। এইটা আমার একটা পছন্দের মাধ্যম। একটা মাস্টারপিস তার নিজের যে কনটেক্সট, তার সাথে আমার কনটেক্সট যখন যোগ হয় তখন আলাদা একটা মাত্রা পায়। তার সাথে সাথে, যে-কোনো ছবিই যেহেতু তার সমসাময়িক ইতিহাসের অংশ, সময়ের ইন্টারপ্রিটেশন, ম্যানিপুলেশনর মাধ্যমে অই ইতিহাসে অই ইতিহাসকে নিয়ে আমার ইন্টারপ্রিটেশনও যুক্ত হয়। এইভাবে অই আর্টওয়ার্কটিরও নতুনভাবে প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়। একমাত্রিকতার বদলে বহুমাত্রিকতাও তৈরি হয়। ধরেন মোনালিসাকে কেউ যদি বোরকা পরায় দেয় বা শাড়ি, তা ভিঞ্চিরতো থাকেই, সাথে বাংলাদেশিও হয়ে ওঠে। ভেনিসের মোনালিসা তখন শাড়ি-বোরকার মাধ্যমে আমাদের পাশের ঘরের মর্জিনা বা মীনাক্ষি হয়ে উঠেন। অপরিচিত থাকেন না। তবে সবসময় যে আমার কনটেক্সটে যুক্ত করতেছি তা নয়, অনেক সময় অই পেইন্টিং বা আর্টওয়ার্কের যে-আপাত নিরীহ ভাব, যে-নিষ্পাপ বিউটি, তাও ‘নষ্ট’ করতে চেয়েছি। তাকে আমার সময়ের রাজনীতিতে যুক্ত করতে চেয়েছি। এ-কারণেই হয়তো ভ্যান গঘের স্টারি নাইট-এর রঙিন তারাজ্বলা আকাশে একটা যুদ্ধবিমান বসায় দিয়ে দেখতে চাইছি তার সৌন্দর্য বাড়ে না কমে। বলা ভালো, এসব নতুন কিছুই নয়।
ছিল ভুল বানানও। প্রচলিত ব্যাকরণ বইয়ের বাক্য নিমার্ণের বাইরে গিয়ে লেখা। ভুল সিনট্যাক্সে। পাবলিশ হবার পর কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কী রকম ইতিহাস? রেফারেন্স কী? সত্যতা কী? এই যে আমাদের সত্যতার আশা ইতিহাসের প্রতি, এটা তো আদতে তৈরি করা। রাজনৈতিকভাবেই তৈরি করা।
আজকে থেকে প্রায় ষাট বছর আগেই মার্শেল দুশ্যাম্প মোনালিসার মুখে গোঁফ এঁকে দিছিলেন। বাচ্চারাও করে এমন। দুশ্যাম্পকে না চিনেই। পাঠ্যবইয়ের রবীন্দ্রনাথের চোখে চশমা পরায় দেয়, নজরুলকে দাড়িঅলা। তো, দুশ্যাম্পের এত বছর পরে কেউ যদি মোনালিসারে কালী বানায় দেয় বা খনা, টেকনিক হিসাবে তা নিশ্চয়ই নতুন হবে না। কিন্তু আইডিয়াটাতো ভিন্নই। তবে এইসবকে আর্ট হিসাবে এখনো অনেকে মানতে পারেন নাই। চারুকলার বাইরের লোকজনতো বটেই, খোদ আর্টের লোকজনের মাঝেও এমন আছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। দু’হাজার বারো-তেরো সালের দিকে। আমি ঢাকা শহরে তখনো নতুন। এক বইমেলায় একজনের সাথে পরিচিত হচ্ছি। প্রাথমিক পরিচয়ের পর উনি (প্রচ্ছদ শিল্পী) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি চারুকলায় পড়েছেন? হ্যাঁ বললাম। কী কী শিখায় আপনাদের? তাও বললাম। উনি শুনে হতাশ হলেন। এগুলা শিখলে পরে তাহলে অন্য পেইন্টিংকে জোড়াতালি দিতে হবে কেন! আমার ধারণা অনেকেই এমন ভাবেন। অনেকে কম্পিউটার-ভিত্তিক বা কোনো ডিভাইসে আঁকারেও ঠিক মানতে পারেন না। তাদের কাছে ডিজাইন-টিজাইন হলে একটা বিষয়, সিরিয়াস(!) আর্টওয়ার্ক কেন ডিভাইসে আঁকা হবে! অনেকে আরো ইমোশনাল; ‘হাতে রঙ না লাগলে পেইন্টিং হয়!’


এইবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। বলতেছিলাম, পেইন্টিং করাকরির শুরু থেকেই পেইন্টিংয়ে টেক্সট ইউজ করতাম। পেইন্টিংয়ে টেক্সট ইউজতো নতুন না। সেই গুহাচিত্রের সময় থেকে ইমেজ এবং টেক্সট হাত ধরাধরি করে হাঁটতেছে। প্রচুর আর্টিস্ট আছেন এমন। বাংলাদেশেও কম নাই। হাশেম খান, ওয়াকিলুর রহমান, মোস্তফা জামান, ইয়াসমিন জাহান নূপুর, নাজমুন নাহার কেয়া, আবীর সোম, মিজানুর রহমান সাকিব উনাদের কথা মনে আসতেছে এই মুহূর্তে। আমাদের ক্যাম্পাসের সিনিয়রদের মধ্যে নির্ঝরদাকেও (নির্ঝর নৈঃশব্দ্য) দেখতাম পেইন্টিংয়ে টেক্সট ইউজ করতে। উনার একটা ইনফ্লুয়েন্সও থাকতে পারে আমার উপর। শুরু দিকে র্যান্ডমলি যা মনে আসতো লিখে যেতাম। তার উপর পরে আঁকতাম। এইভাবে আঁকার ফলে যেইটা হত, টেক্সটটা টেক্সচার হয়ে যেত। পরে এই টেক্সচার যেহেতু চাচ্ছিলাম না, এইরকম টেক্সটের বদলে নির্দিষ্টভাবে টেক্সট ইউজ করতে থাকি। মানে সবখানে না, শুধু নির্দিষ্ট জায়গাতেই টেক্সট বসতে লাগল। এতে টেক্সটও ইমেজের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। মনে আছে একটা পেইন্টিংয়ে কাফকার মেটামরফিসিস থেকে লিখছিলাম। গ্রেগর সামসার পোকা হয়ে যাওয়াটা। ঝুঁকতেছিলাম অ্যাবসারডিটির দিকেও। অই সময় একটা সিরিজ ছিল ‘ওয়েটিং ফর গডো’ নামে। বেকেট দ্বারা ইন্সপায়ারড হয়ে। কোথাও কোথাও ভুল অংকও লিখতাম। ১২+৩=৭ এই টাইপের। আমাদের অভ্যস্ত যে লজিক সিস্টেম, তাকে না মানার উদ্দ্যেশে। আরো পরে শুধু টেক্সটকেই আর্টওয়ার্ক হিসাবে নিলাম। কখনো শুধু একটাই টেক্সট। একটা মাত্র বাক্য। ব্যানার বা পোস্টার আকারে। লিফলেট হিসাবেও। কীরকম টেক্সট? র্যান্ডমলি লিখে যাওয়া অসংলগ্ন, ভুল বানানের, ভুল সিনট্যাক্সের বাক্য। এসব বাক্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাহিত্যিক কনটেক্সটের সাথে কানেক্ট করে বটে, তবে মোটাদাগে অর্থহীন। পুরিপুরিই। কারণ কী? প্রথমত আমাদের যে অভ্যস্ততা-আর্কষণ, একরকম পবিত্র ভক্তিও আছে শুদ্ধ বানান-বাক্যের প্রতি, তাকে বিশৃঙ্খল করা। অর্থপূর্ণতা-লজিক-রিজনের প্রতি আধুনিক যে বিশ্বাসব্যবস্থা, তার প্রতি অবিশ্বাসই এইসব পোস্টার-লিফলেটের মূল প্রণোদনা।
মানে এক মাধ্যমের সাথে আরেক মাধ্যমের সহাবস্থানে যাদের আপত্তি, তাদের বিষয়টা তেমন একটা পছন্দ হবে না। কিন্তু আমি সচেতনভাবেই এই বাউন্ডারি এড়াতে চাই। এই এড়ানোর ফলে যেটা হয়, ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গির কারণে আর্টওয়ার্কটা বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, বক্তব্যটাও জোরালো হয়ে ওঠে।
একবার চেরাগি আর্টশো’তে, যেইটার আয়োজক ছিল যোগ আর্ট স্পেস, তাদের আয়োজনে একটা বিজ্ঞাপন ছাপাইছিলাম। দৈনিক আজাদীতে। চেরাগি পাহাড়ের ইতিহাস নিয়ে। সাথে ইজিপশিয়ান একটা ড্রয়িং। এই বিজ্ঞাপনে লিখা ইতিহাসও বলাবাহুল্য সত্য ছিল না। ছিল ভুল বানানও। প্রচলিত ব্যাকরণ বইয়ের বাক্য নিমার্ণের বাইরে গিয়ে লেখা। ভুল সিনট্যাক্সে। পাবলিশ হবার পর কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কী রকম ইতিহাস? রেফারেন্স কী? সত্যতা কী? এই যে আমাদের সত্যতার আশা ইতিহাসের প্রতি, এটা তো আদতে তৈরি করা। রাজনৈতিকভাবেই তৈরি করা। আমরা যে-ইতিহাস জানি তার কতটুক সত্য? এই সত্য মাপার পাল্লাই বা কোনটা? তারচেয়ে বড় কথা এটা আসলে কার ইতিহাস? কার সত্য? রাজার না প্রজার? জয়ীর না পরাজিতের? কে লিখতেছে আসলে? এ-প্রশ্নগুলোসহ ইতিহাসকে দেখতে পারলে মনে হয় ইতিহাসের প্রতি মোহ কমবে। যেইটা জরুরিও। মানে মোটাদাগে বললে।
আরো একটা বিষয়, নিজের টেক্সটের পাশাপাশি আরো নানান জায়গার টেক্সট আমার আর্টওয়ার্কে ইউজ করে থাকি এবং বিনা দ্বিধায়। এরকম ইন্টারভিউ থেকেও নিয়েছি। ইন্ডিয়ান এক্ট্রেস শ্রীলেখা মিত্র থেকে জয় গোস্বামী, সিনেমার ডায়ালগ-সাবটাইটেলসহ নানান জায়গা থেকে । বলা বাহুল্য, বাংলা টেক্সটেই আমার আগ্রহ বেশি থাকে। বিশেষ করে সেই সব টেক্সট যেগুলোকে আমরা হরহামেশা নানানভাবে ফেস করি, আমার ধারণা, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানান অর্থহীনতাকেই অইসব টেক্সট বেশি তুলে ধরে। আমার ব্যবহৃত নানান ইমেজের সোর্স খেয়াল করলেও এই বিষয়টা বুঝা যাবে। নানান ওপেন সোর্স থেকেই ইমেজ সংগ্রহ করি। হিন্দি-বাংলা সিনেমা থেকে শুরু করে এনিমেশন, সাহিত্য, বিজ্ঞাপন, পোস্টার পত্র-পত্রিকা, ইতিহাস বই, বিখ্যাত ফটোগ্রাফ, রাজনৈতিক চরিত্র, সাহিত্যিক চরিত্র, গেমস ক্যারেক্টার, ভাইরাল চরিত্র, অনলাইনের বিভিন্ন আইকন, ইমোজি সবই আছে। কখনো আলাদা আলাদাভাবে আছে, কখনো আছে যৌথভাবে। পাড়া বা মহল্লার মতোন যেন। এগুলোকে বির্নিমাণের মাধ্যমে নতুন অর্থ দেয়ার চেষ্টা করি। আমাদের পারিপার্শ্বিকতার সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করি। বলা ভালো, আমার টুকটাক লেখালেখির অভ্যাস আছে। ধারণা করি, এই লেখালেখির প্রভাবটাই আমার ভিজ্যুয়াল আর্ট প্র্যাকটিসে পড়েছে। যারা আর্টে মাধ্যমের ভার্জিনিটি নিয়ে বেশি সচেতন, মানে এক মাধ্যমের সাথে আরেক মাধ্যমের সহাবস্থানে যাদের আপত্তি, তাদের বিষয়টা তেমন একটা পছন্দ হবে না। কিন্তু আমি সচেতনভাবেই এই বাউন্ডারি এড়াতে চাই। এই এড়ানোর ফলে যেটা হয়, ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গির কারণে আর্টওয়ার্কটা বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, বক্তব্যটাও জোরালো হয়ে ওঠে। যিনি দর্শক, তিনি হয় ইমেজে, না হয় শব্দে অথবা কোনো একটা অবজেক্টে নিজেকে কানেক্ট করতে পারেন। ফলে দর্শকদের আর্টে এক্সেসটা বাড়ে। আর এটাতো পুরানা কথাই, আর্টের এরকম কম্পার্টমেন্টাল হয়ে ওঠার পিছনে একটা রাজনৈতিক ইতিহাসও আছে। এখানে পটুয়ারা যখন পট দেখাতেন তখন গেয়ে গেয়ে দর্শকদের পটের গল্পটাও শুনাতেন। পটের ছবিগুলো একটার পর একটা আসতো। এখানে পটুয়ারা গানটা গেয়ে শোনাচ্ছেন ইমেজের সীমাবদ্ধতার জন্য না। টোটাল প্রদর্শনীটাকে আরো ইন্টারেস্টিং করার জন্য।
আমার রমিজ সিরিজটাও এরকমই অনেকটা। কোনোসময় আগে ছবিটা আঁকা, কোনোসময় টেক্সটটা আগে লেখা।
দর্শকের সাথে যোগাযোগ আরো বাড়ানোর জন্য। আমার রমিজ সিরিজটাও এরকমই অনেকটা। কোনোসময় আগে ছবিটা আঁকা, কোনোসময় টেক্সটটা আগে লেখা। ছবি এবং টেক্সট কেউই কারো অনুগত নয়। সচরাচর ইলাস্ট্রেশন যেমন হয়, ছবি লেখাকে বর্ণনা করে করে যায়, অনুগত থেকে। এখানে তা ঘটে নাই। এখানে টেক্সট এবং ইমেজ স্বাধীন। যে যার মতোন করে এগিয়েছে। টেক্সটের তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এ-ভাষার যারা না, তারা বুঝতে পারবে না। তারপরও টেক্সটের মাধ্যমে, আর যেহেতু আমি বাংলায় লিখি মূলত, এর মাধ্যমে স্থানিকতার সাথে ওতপ্রোত হওয়াটা সহজ হয়। এখন যদি প্রশ্ন করেন, স্থানিকতার মাহাত্ম্য কী? বলবো গ্লোবাল বলতে আদতে কিছুই নাই। ইংরেজিও কি গ্লোবাল? যারা জানেন, তাদের আমলে নিলে গ্লোবাল বটে, কিন্তু না জানার হারই বেশি। তো এই বিচারে, চাঁদ-সূর্য-আকাশ এরকম জিনিসগুলা বাদ দিলে আসলে গ্লোবাল কিছুই নাই। তাই সবই স্থানিক। আর এই উপনিবেশোত্তর সময়ে স্থানিক হওয়াটা অবশ্যই আপনার রাজনৈতিক অবস্থান। জরুরিও।


মূলত আর্ট জিনিসটাই কি রাজনৈতিক নয়? আপনার-আমার আর্ট একজন রিকশাওয়ালা বুঝুক বা না বুঝুক, তার যে বেঁচে থাকা, বলা ভালো টিকে থাকা তার বিরুদ্ধেও যাইতে পারে। ক্ষতিও করতে পারে। অনেক সুক্ষ্মভাবে। তাই আর্টকে যতটুক নিরীহ আপাতভাবে আমাদের মনে হয়, আদতে অতটুক নিরীহ মোটেই নয়। কোনো আর্টই নয়। মূলত আমার রাজনৈতিক অবস্থানকেই স্পষ্ট করেছে আমার আর্ট। হয়তো সরলভাবে না। কোনো কোনো সময় তা হয়তো হেঁয়ালি, কোনো কোনো সময় হয়তো বেশ অস্পষ্ট-দুর্বোধ্য, আমার নিজের কাছেও অনেকসময়, কিন্তু তারপরও তা রাজনৈতিকই। পরে হয়তো খোলাসা হবে, সময় নিবে হয়তো, যদি টিকে থাকে, তারপরও তা আমার যাপিত সময়কেই ধারণ করছে। ভাষা, মাধ্যম, তার রিপ্রেজেন্টশন নিয়ে তর্ক হতে পারে, হওয়াটা জরুরিও, স্বাস্থ্যকরও। তারপরও তা এই সময়ের শিল্প। আমার সময়ের শিল্প। আমাদের সময়ের শিল্প।
ধরুন, এক লোক, তিনি পাগল, বন্দি হইয়া আছেন গারদে, টাইম পাসের জন্য তিনি একখানা কয়লা কুড়ায় নিয়ে আঁকতে থাকেন গারদের দেয়ালে, যে আঁকাআঁকি আপাত হাবিজাবি আপনার কাছে, কিন্তু অই পাগলের কাছে অই টাইমে অইটাই মোকাবিলার অস্ত্র, লুকানোর পরিখা (যেহেতু শহিদ হবার মতোন এনাফ বেকুবি বা সাহস উনার চিত্তে নাই), যাহা পলিটিক্যাল কারেক্টসনেসের লাল কলমে আপনি ভুল হিসাবে দাগায়া দিলেও উক্ত পাগলের কাছে রাইটই। অন্তত সাময়িক। আবার সাময়িক আনন্দরেও যারা মহাকালের পাল্লায় তুলে দেন, তাহাদের অগ্রিম বলি, কালের হিসাব সকলের সমান না। অনেক জীবের জীবনে ঘড়িও নাই। এমনকি সময়ও হয়তোবা। সো, হোয়াই আর ইউ ওরিড?
এইটুকুই।
পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।